বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:২৮ অপরাহ্ন
ঈদ, একুশে এবং বাঙালির ঘরে ফেরা
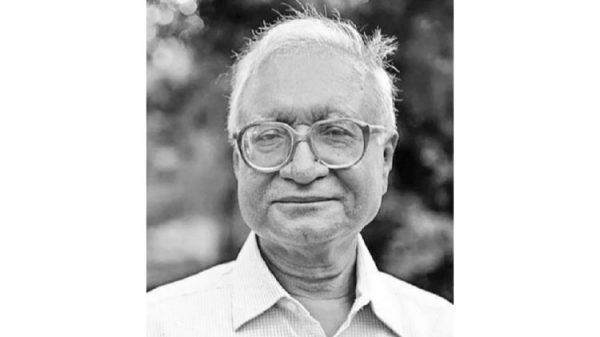
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী:
এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে ঈদ আর তেমন ঐক্যের অনুষ্ঠান নয়। তবুও ঈদ তো মাত্র দু’বার আসে বছরে। একুশে ফেব্রুয়ারি কোনো উৎসবের দিন নয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে উৎসবের উপলক্ষে পরিণত করলে বরং অপমান করা হয় শহীদদের, অমার্যাদা ঘটে এর তাৎপর্যের। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিন, ঐক্যকে দৃঢ় করবার দিন। যখন দেখি যে, আত্মদানের স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, যখন দেখি অসংখ্য মানুষ এগিয়ে এসেছে, যখন শোনা যায় ঘুম ভেঙেছে চতুর্দিকে, ফুলের মালায় গানের কলরবে তখন একটা নতুন সংবিতকে দেখতে পাই, একটা নতুন সম্পর্ককে চিনতে পারি। ঐক্যসৃজনকারী তাৎপর্যে ঈদের অনুষ্ঠান থেকে এই দিন উদ্যাপন ভিন্ন, কেননা এতে আমরা শুধু যে আত্মীয়-পরিচিতের সঙ্গে মিলিত হই তা নয়, অনেক অপরিচিত, অচেনা মানুষের সঙ্গে একটা ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত হয়ে উঠি আলিঙ্গন না করেও। এই দিনে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো চেতনা নেই, একটা অনুভবের মধ্য দিয়ে অন্যের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাই, নিজেকে অনেক দূর বিস্তৃত করে দিই। এই ঐক্য ধর্মনিরপেক্ষ, শুধু এই কারণে বা এই অর্থে নয় যে, পার হয়ে যাই আমরা সাম্প্রদায়িক ব্যবধানের প্রান্তসীমা, বরং এই অর্থে আরও বেশি যে, ধর্মের ধর্মীয় সীমা, অর্থাৎ এর জগৎবিমুখ আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিকতা, পার হয়ে আমরা হয়ে উঠি জাগতিক ও ইহলৌকিক। একুশে ফেব্রুয়ারির মতো ধর্মনিরপেক্ষ দিন বাংলাদেশে কম আছে, কবর জিয়ারত সত্ত্বেও। অন্যদিনটি হলো পহেলা বৈশাখ।
দেখি যার সঙ্গে আজিমপুরে দেখা হয়েছিল, তার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছি শহীদ মিনারের নিচে, অথবা পরবর্তী কোনো সভা-প্রাঙ্গণে। যে-সংকলন এক জায়গায় কিনেছি সেই সংকলন অন্য জায়গাতেও বিক্রি হচ্ছে। সেই একই বক্তা একই কথা বলছেন, যা গত বছরেও বলেছিলেন, যা আগামী বছরেও হয়তো বলবেন। সেই একই লেখা, একই ধরনের লেখা। একই প্রকাশ, একই অনুষ্ঠান। তখন মনে হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে-একটা জাগরণ এসেছে হৃদয়ে, যে-জাগরণ গুঞ্জরণ করছে ভেতরে, আমার ভেতরে, অন্যের ভেতরে, সবার ভেতরে, সেটা যেন আটকা পড়েছে একটা জালে-ঘেরা খাঁচায়, কিছুতেই পথ পাচ্ছে না বের হয়ে যাওয়ার, অথচ বের হয়ে যেতে তার ভীষণ আগ্রহ, বহির্গমনের আয়োজনে একটা র্থ র্থ অস্থিরতা। এই কথাটা ভাবতেই খুব দুঃখ হয়, খেয়াল হয়, মহৎ অনুভবের এ কি অসামান্য অপচয়, প্রাণচাঞ্চল্যের এ কি নিদারুণ ব্যর্থতা। তখন এও বোঝা যায় যে এই অনুভবের, এই চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা সর্বক্ষণই ছিল, আমরা টের পাইনি, আমরা তাকে কাজে লাগাইনি। কাজে না লাগানোর গ্লানিটা তখন খুব বড় হয়ে বাজে। সন্দেহ হয় অনুপ্রেরণা শেষ পর্যন্ত ফুঁসে-ওঠা আতশবাজির মতো অবসিত নিষ্প্রাণতায় পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়বে, একুশে ফেব্রুয়ারির তাজা ফুলগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে আবার আমরা ছোট ছোট ঘরে ফিরে আসব : উন্মুক্ত প্রান্তরে যারা মিলেছিলাম তারা সামান্য কুটিরবাসী দিনানুদৈনিকতার ভেতর ঠিকানাবিহীন হয়ে হারিয়ে যাব।
অনুভব ও অনুপ্রেরণা যে প্রকাশের পথ পাচ্ছে না তার একটা প্রমাণ ও লক্ষণ তো এই যে, ভেতরের চাঞ্চল্যকে আমরা বাইরের কোনো অনুষ্ঠান কি প্রতিষ্ঠান, সৃজন কি উদ্ভাবনের ভেতর প্রতিফলিত করতে পারিনি। উৎসাহ প্রত্যক্ষ অবয়ব গ্রহণ করেনি। সাহিত্যই বলি কি সামাজিক পরিবর্তনই বলি, কোনো বড় কাজের ভেতর আমাদের প্রাণের যে-অস্থিরতা তা সৃষ্টিশীল প্রতিরূপ লাভ করতে পারেনি।
তার চেয়ে কম মর্মান্তিক নয় এই সত্য যে, দেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় খুব অল্পলোকের জীবনেই একুশে ফেব্রুয়ারি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আমরা জানি এই দিনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হব কিন্তু সেই ঐক্য-চেতনা ক’জনের? সমাজের কত বড় এলাকায় তার বিস্তার? একুশে ফেব্রুয়ারি তো শিক্ষিত মানুষের অনুষ্ঠান, আর দেশে শিক্ষিত মানুষ ক’জন? তাই দেখা যায় শহরেই থাকে এই দিনটি আবদ্ধ। গ্রামে যে যায় সেও গ্রামের বিদ্যালয়টি পর্যন্তই। অল্প ক’জনের জন্যই এই সর্বজনীন অনুষ্ঠানটি আসে। বাদ-বাকি যারা তারা হয় দর্শক, নয়তো এ বিষয়ে বেখবর। অর্থাৎ শুধু যে ধনী-নির্ধনের তফাৎটাই আবার নতুন করে প্রকট হয়ে ওঠে তা নয়, আরও একটা বৈষম্য চোখে পড়ে শিক্ষার বৈষম্য, সংস্কৃতি-চর্চার বৈষম্য। একুশে ফেব্রুয়ারি তুলনায় বিত্তবান যারা তাদের জন্যই, শিক্ষিত যারা, যারা চিৎকর্ষের কারিগর তাদের কাছেই এর মূল্য।
একুশের এই জাগরণ যে সর্বগ্রাসী হতে পারছে না তার কারণ কী? অন্তরায়টা কোথায়? একটা প্রধান অন্তরায় অবশ্যই ধনবৈষম্য, যে-কারণে ঈদের চাঁদ সব গৃহে সমান আলো বিতরণ করতে ব্যর্থ হয়। আরও একটা অন্তরায় হচ্ছে ভাষা। প্রথমত, বিদেশি ভাষার একটা অনেক বড় পাথর আছে দরজার ওপর চাপা। এই ভাষাতেই আমাদের ভাবনা-চিন্তা বলা-কওয়া; এক সময় ছিল যখন এতেই চলত আমাদের স্বপ্নদেখা। এই ভাষাটা দেশের না এ-ভাষা শিক্ষিতরাও বোঝেন না ঠিকমতো, ব্যবহার করতে পারেন না যথার্থরূপে। এই অসম্ভব পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্যই দরকার। সে-কথা আমরা বলছিও। পরিবর্তন হচ্ছেও, ধীরে ধীরে।
পরিবর্তনটা শুধু একটা অবস্থার নয়, পরিবর্তন একটা মনোভঙ্গিরও। সেই জিনিসটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনে ভাষা ছিল একটা বৈষম্যের প্রতীক। যেহেতু স্থানীয় মুসলমানরা ক্ষমতার সিঁড়িগুলোতে বসবার সুযোগ পায়নি তাই স্থানীয় মানুষের ভাষা কখনো আভিজাত্যের গৌরবচিহ্ন অর্জন করেনি। বাংলা কখনো রাজভাষা ছিল না। সেই জন্যই যারা অভিজাত, যারা বীর বলে সম্মানিত তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করা দূরে থাক, বরং বাংলা যে জানেন না এই খবরটাকে উঁচু গলায় প্রচার করেছেন। যারা গৌরবান্বিত তারা বাংলা জানতেন না, তাই যারা সেই গৌরবের আলো নিজেদের গায়ে মেখে নিতে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন তারাও বলেছেন, দেখো, দেখো, বাংলা আমার ভাষা নয়। এককালে আভিজাত্যের ভাষা ছিল ফার্সি, পরে উর্দু, তারও পরে ইংরেজি। অর্থাৎ কিনা বীর যারা তারা সবসময়েই দেশ থেকে দূরে থেকেছেন, এবং যিনি যত দূরে থাকতে পেরেছেন তার বীরত্ব ততো নিঃসংশয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি বাংলাকে গ্রহণ করি তাহলে এই মনোবৃত্তিতেও পরিবর্তন আসবে।
এখনো আসেনি। এখনো সামাজিক পর্যায়ে বীরের সম্মান তাদের জন্যই তুলে রাখি যাদের মুখে বাংলা ভাষা অহরহ উচ্চারিত হয় না। ইতিমধ্যে গাড়ির নম্বরে, দোকানের সাইনবোর্ডে, চিঠির প্যাডে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হোক এই কথাটা খুব করে বলছি। ব্যবহার হচ্ছেও, আরও হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই যে গাড়ি, বড় দোকান, চিঠির প্যাড এই সব একটা নির্দিষ্ট এলাকারই ব্যাপার, শহরের একটা অংশেই এসব বস্তুর বিশেষ সংস্থান, সেই অংশে যেখানে বিত্ত ও সংস্কৃতি প্রায় যমজ ভাইয়ের মতো সানন্দে বসবাস করছে।
দেশের অধিকাংশ মানুষ এমনকি বাংলা ভাষার ব্যবহারও জানে না। কাজেই ভাষা-সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। বাংলা চালু হওয়া মাত্রই যে হঠাৎ করে দেশের অধিকাংশ মানুষের একটা খুব উপকার হবে এমন আশা করা যায় না। তবে হ্যাঁ, গৃহে প্রত্যাবর্তনের কাজটা শুরু হবে, আমরা দেশমুখো হবো; যে লোক নিজের বাসগৃহ নিয়ে ভয়ানক লজ্জিত ও আত্মসচেতন ছিল তার সেই ম্রিয়মাণ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। আর বিদ্যার্জনও কিছুটা সহজ হবে মাতৃভাষা ব্যবহার করলে যা সব সময়েই হয়ে থাকে। কিন্তু কতটা সহজ হবে সে বিষয়ে যেন কোনো ভ্রান্ত প্রত্যাশা না থাকে আমাদের। টাকার জোরটাই আমাদের সমাজে আসল জোর, সেই জোরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে হয়। এই জোরটা খুব অল্প মানুষের আছে। ভাষার জোর আসার আগে যে টাকার জোর দরকার সেই জোরটা এখনো আসেনি না-আসার ব্যাপারকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের, অতি অবশ্যি।
তবু ঘরের দিকে চোখ ফেরানোর ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত শুভসূচনা; ঘরের হাল ওই তাকানো থেকেই ফিরতে পারে। বলা বাহুল্য, এখনো আমরা ঘরের দিকে ভালো করে, পুরোপুরি তাকাতে অভ্যস্ত হইনি। হইনি যে তা বোঝা যায় আমাদের খবরের কাগজগুলোর প্রথম পৃষ্ঠার দিকে তাকালেই। যে-কাগজটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেটি বাংলা কাগজ নয়, আর ইংরেজি কি বাংলা সব খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক সংবাদের ছড়াছড়ি। এত বেশি মেকি আন্তর্জাতিকতাপনা অন্য কোনো দেশে আছে কি-না খুব সন্দেহ। এককালে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের পরীক্ষায় প্রার্থীদের জ্ঞান দেখা যেত বিদেশের ব্যাপারে ভীষণ চৌকস, স্বদেশের ব্যাপারে অনেকটা সংকুচিত। এখনো তা-ই সর্বত্র যোগ্যতা বিচারের মানদ-, ওই নানান খবর একেবারে নখদর্পণে রাখতে পারাটা।
ঘরে ফেরাটা খুব দরকারি কাজ, কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে দেখা দরকার হবে যেন আমরা ঘরে ফেরাটাকেই যথেষ্ট মনে না করি। যেন এমন অবস্থা না হয় যে অভিমান করে দরজা দিলাম বন্ধ করে, অর্জন করলাম না নতুন সম্পদ, যা ছিল পিতা-পিতামহের আমলের তার ওপরেই ভরসা করে রইলাম বেকার হয়ে। ঘরে ফিরব ঘরে থাকার জন্য, বেকার হওয়ার জন্য নয়। ঘরে ফিরে ঘরের অবস্থান পাল্টে দেব। জমানো বিত্ত কখনো যথেষ্ট নয়, বিত্ত সৃষ্টি করা প্রয়োজন নতুন করে, প্রতিনিয়ত, অনলস সাধনায়।
ভয়েস/আআ
























